মাহমুদুল হাসান (ছদ্মনাম) ঢাকায় বাস করতেন। তিনি একটি একাডেমিক প্রকাশনীতে লেখক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন দেশের একটি নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতেন। বছর খানেক আগে জানতে পারলেন তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। শুরু হলো জীবনযুদ্ধ। অথচ যার অধীনে তিনি চিকিৎসা নিতেন তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি রোগী দুরারোগ্য এ ব্যাধিতে আক্রান্ত।
ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার দু-তিন মাসের মধ্যে তিনি মারাও যান। অপারেশন-ক্যামোথেরাপিসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটাতে গিয়ে জীবনের কষ্টার্জিত সব অর্থ ব্যয় করেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঋণগ্রস্ত হয়ে অবুঝ দুই শিশু আর স্ত্রীকে অতল সাগরে ভাসিয়ে পাড়ি জমালেন পরপারে।
তার স্ত্রী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সময় সংবাদকে বলেন, ‘আমার স্বামীর হঠাৎ ক্যানসার ধরা পড়ার পর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তার চিকিৎসা করাতে গিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। স্বামী বেঁচে থাকলে তাও একটা সান্ত্বনা থাকতো। ছোট দুটো বাচ্চা নিয়ে মাঝ সাগরে পড়েছি। কী করব জানি না।’
রিনা আক্তার নামে এক গৃহিণী যশোর থেকে ঢাকায় এসেছেন গ্যাস্ট্রোলিভারের চিকিৎসক দেখাতে। এলাকায় অনেক চিকিৎসক দেখিয়েছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। যখনই কোনো নতুন চিকিৎসকের কাছে গেছেন, তখনই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নতুন নতুন ওষুধ দিয়েছেন। পুরাতন রিপোর্ট দেখতে চান না নতুন চিকিৎসক। নিরুপায় হয়ে এবার এসেছেন ঢাকায়।
রিনা আক্তার বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছি। তারা নতুন নতুন টেস্ট আর ওষুধ দেন। সেগুলো খেয়ে কিছুদিন ভালো থাকি। তারপর আবার শুরু হয় সমস্যা। ডাক্তার পরিবর্তন করলেই নতুন পরীক্ষা। পুরাতন রিপোর্টগুলো আর দেখে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমার স্বামী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ঢাকাতে এসেছি; এখানে পরিচিত কেউ নেই যে, তার বাসায় উঠব। স্বল্প খরচের একটি হোটেলে উঠেছি। কদিন থাকতে হবে জানি না। বাড়িতে বাচ্চাটাকে রেখে এসেছি। এবার সুস্থ না হলে হয়তো মরতেই হবে।’
এমন গল্প আমাদের সমাজে অহরহ। অথচ চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকার মেটাতে গিয়ে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ নিঃস্ব হচ্ছেন। অভাবের আগুনে পুড়ছে অনেক সুখের সংসার।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বৈশ্বিক এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে ২৪ শতাংশ মানুষ ‘বিপর্যয়মূলক’ ব্যয়ের মধ্যে পড়ছেন। এছাড়া চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতিবছর ৬২ লাখের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছেন এবং ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে ১৬ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা নেয়া থেকে বিরত থাকেন। অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রয়োজন হলেও চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে যান না।
এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগনিয়ন্ত্রণ বিভাগের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. বেনজির আহমেদ সময় সংবাদকে বলেন, চিকিৎসা ব্যয় কমিয়ে আনতে প্রথমত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। উন্নয়নের একটি বড় অংশ স্বাস্থ্য। রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রিজের পাশাপাশি জনগণের স্বাস্থ্য যদি না থাকে তাহলে উন্নয়ন টেকসই হবে না।
তিনি আরও বলেন, দেশের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ ভাবে বাড়াতে হবে। এখন আছে ৪ শতাংশ, এটা অন্তত ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। যাতে একজন মানুষ অসুস্থ হলে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সরকারি হাসপাতাল থেকে নিতে পারেন। এতে মানুষের পকেট থেকে চিকিৎসা ব্যয় কমে আসবে। এরপর হলো ওষুধ। চিকিৎসকরা যত ওষুধ লিখবেন সেটা যদি হাসপাতাল থেকে দেয়া যায়। সেক্ষেত্রেও চিকিৎসা ব্যয় কমে আসবে। অপারেশন বা ক্যানসারের ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়, এসব রোগ ‘বিপর্যয়কর’ স্বাস্থ্য ব্যয়। এগুলোও যদি হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে স্বাস্থ্য ব্যয় কমে আসবে। উন্নয়ন টেকসই হবে এবং বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবে স্বাস্থ্য সেবায়।
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে বাধা
বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে সবচেয়ে বড় বাধা এ স্বাস্থ্যখাত। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে ২০৩২ সালের স্বাস্থ্য ব্যয় ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য থাকলেও বতর্মানে রয়েছে তার প্রায় দ্বিগুণ। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল ৬৪ শতাংশ। এ ব্যয়ের অঙ্ক কমার পরিবর্তে ২০২০ সালে আরও বেড়ে যায়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস (বিএনএইচএ) ১৯৯৭-২০ অনুসারে, ওই বছর বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল ৬৯ শতাংশ।
২০১২ সালে বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয় ছিল ৬২ শতাংশ। সে বছরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করে, যার লক্ষ্য ছিল ২০৩২ সালের মধ্যে আউট অব পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় ৩২ শতাংশে কমিয়ে আনা।
কিন্তু এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আউট অব পকেট ব্যয় ধীরে ধীরে কমে আসার কথা থাকলেও ঘটছে তার উল্টোটা। অর্থাৎ কমার বদলে প্রতি বছর বাড়ছে এ ব্যয়, যা মধ্যম আয়ের দেশের ধারণার বিপরীত। কারণ আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশের তুলনায় মধ্যম আয়ের দেশে কম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের যে আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার, তা দরিদ্র দেশের পর্যায়ের।
গ্লোবাল হেলথ এক্সপেনডিচার ডেটাবেজ, হু এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস অনুসারে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি কেবল যুদ্ধবিদ্ধস্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত আফগানিস্তানের।
আরও পড়ুন: স্বাস্থ্যখাতে জনগণের নিজের ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
২০১৮ সালে আফগানিস্তানের আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার ছিল ৭৯ শতাংশ। এর পরেই আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার সবচেয়ে বেশি ছিল বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ।
বলা হচ্ছে, ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। আর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে ২০২৬ সালে।
ব্যক্তির খরচ কোথায়
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট বলছে, রোগীরা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয়ের ৬৪.৬ শতাংশ ওষুধের জন্য, ১১.৭ শতাংশ ল্যাবরেটরির খরচ মেটাতে, ১০.৪ শতাংশ চিকিৎসকের ভিজিটে, ২.৪ শতাংশ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্র্যাকটিশনার, ০.৩ শতাংশ ডেন্টিস্টদের খরচে, ১০.১ শতাংশ হাসপাতালে এবং ০.১ শতাংশ চিকিৎসা পণ্য কিনতে ব্যয় করছেন।
এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ সময় সংবাদ বলেন, ‘যখন চিকিৎসা ব্যয় সরকার বহন করে তখন সরকার চাইবে না কেউ এক্সেস মেডিসিন কিনুক, অতিরিক্ত টেস্ট করুক। তখন প্রেসক্রিপশন ছাড়া মেডিসিন বিক্রি হবে না। আমাদের দেশে আমরা চাইলেই ওষুধ কিনতে পারি। ওষুধের দাম কিন্তু অনেক বেশি। আমাদের রোগীদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার হার বেশি, অ্যান্টিবায়োটিকের দামও কিন্তু বেশি। এসব কারণে মেডিসিন খরচ বেশি হয়। আমরা যদি প্রেসক্রিপশন ছাড়া মেডিসিন বিক্রি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার অনেক কমে যাবে।’
অধ্যাপক আব্দুল হামিদ বলেন, ‘মেডিসিনের পর টেস্টে খরচ বেশি হয়। সরকার চাইলে সেটিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো হাসপাতালে কত টেস্ট হয় তার কোনো মনিটরিং নেই। আমরা কিন্তু জানি না একজন ডাক্তার বছরে কোন ডিজিজের জন্য কত টেস্ট দিয়েছে। এটি যদি অনলাইনে মনিটর করা যায়, তাহলে বুঝতে পারব কোনো প্রাইভেট হাসপাতালে বেশি করে ডায়াগনস্টিক টেস্ট হচ্ছে কিনা। এটা করা যাচ্ছে না বলে আমরা বলতে পারছি না, এ টেস্টটা পেশেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় কিনা। এসব রেগুলেশন প্রপারলি না করার কারণে আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার কমছে না।’
তিনি আরও বলেন, মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হলে অন্য ডিজিজগুলো ভালোভাবে ম্যানেজ করা যাবে। তখন হেলথ স্ট্যাটাস বেড়ে যাবে। সিজারিয়ান সেকশন, ম্যাটারনাল ডেথ কমে যাবে। যখন ফ্যাসিলিটিতে জনবল থাকবে, মনিটরিং থাকবে, তখন হেলথ সার্ভিসের অন্যান্য ইন্ডিকেটর ভালো হবে।
কে, কত ব্যয় করছে
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের মাথাপিছু ব্যয় বাড়ছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য ব্যয় ৫৪ মার্কিন ডলার। ১ ডলার ৮৪.৭৭ টাকা হিসাবে যা ৪ হাজার ৫৭৮ টাকা। ২০১৭ সালে তা ছিল ৩৭ মার্কিন ডলার এবং ২০১৪ সালে ছিল ৩৩ ডলার। বর্তমানে ব্যয় বাড়লেও তা শ্রীলঙ্কা বা মালদ্বীপের চেয়ে কম।
প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে স্বাস্থ্য খাতে দেশে মোট ব্যয় হয়েছিল ৭৭ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ব্যক্তির ব্যয় ছিল ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ, সরকারের ছিল ২৩ দশমিক ১ শতাংশ, উন্নয়ন সহযোগীদের ব্যয়ের পরিমাণ ৫ শতাংশ। বাকি ৩ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওর।
প্রতিবেদনে ১৯৯৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সরকারের অংশের ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমছে এবং ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।
স্বাস্থ্য খাতে সরকার যে ব্যয় করে, তার ৯৩ শতাংশ আসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে আসে ১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং বাকি ৫ দশমিক ৪ শতাংশ আসে অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে।
ওষুধে খরচ বেশি
চিকিৎসা করাতে গিয়ে ওষুধের পেছনে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় মানুষের। প্রায় ৬৪ দশমিক ৬ শতাংশ অর্থ খরচ হয় ব্যক্তির পকেট থেকে। বাকি অর্থ ব্যয় হয় রোগনির্ণয় বা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা–নিরীক্ষা, চিকিৎসক দেখাতে, হাসপাতালে ভর্তি এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সেবা নিতে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সায়েদুর রহমান সময় সংবাদকে বলেন, চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে চিকিৎসার একটা বড় অংশ ওষুধের ব্যয়। আর এর পুরাটাই খরচ হচ্ছে ব্যক্তির পকেট থেকে।
তিনি বলেন, ‘অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে সর্বনিম্ন বরাদ্দ হয়। ফলে চিকিৎসা ব্যয় মানুষের পকেটের ওপর পড়ে। রাষ্ট্র যদি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দায়িত্বটা নেয় তাহলে চিকিৎসা খরচ অনেকাংশে কমে যাবে। এ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সংখ্যাও খুব বেশি নয়, মাত্র ২৫০-৩০০টির মতো। এ ওষুধগুলো যদি রাষ্ট্র নিজে প্রস্তুত করে তাহলে তিনটি সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, মানুষ যৌক্তিক দামে সেসব ওষুধ কিনতে পারবে; দ্বিতীয়ত, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে থাকবে; এবং তৃতীয়ত, প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ সরবরাহের কারণে অনেক দামি ওষুধ লেখার যে প্রবণতা, সেটা কমে যাবে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজার রয়েছে। সরকার যদি ৫ হাজার কোটি টাকার ওষুধ কেনে, তাহলে মানুষের পকেট থেকে যে ২৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়, সেটা ১৫ হাজার কোটিতে নেমে আসবে। অর্থাৎ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় কমে আসবে।
সম্প্রতি সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, ক্যানসার, কিডনি রোগ বা পক্ষাঘাতের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেকে শেষ সম্বল ভিটা বা জমি বিক্রি করেন। এসব রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অনেকে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছেন। ওষুধ কোম্পানিগুলো আগ্রাসী বিপণন নীতি পরিহার করলে, দামি মোড়ক ব্যবহার না করলে, উপহার দেয়া বন্ধ করলে ওষুধের দাম কমবে।
‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমাতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতার বিষয়ে জোর দিয়েছে। এছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি বাড়াতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ কম খরচে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পায়। তাহলেই চিকিৎসা ব্যয় গড়ে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে চলে আসবে,’ যোগ করেন অধ্যাপক সায়েদুর রহমান। সূত্র: সময় সংবাদ




















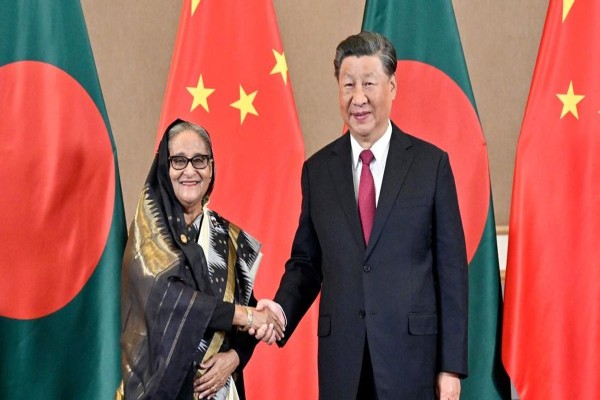


মন্তব্য করুন